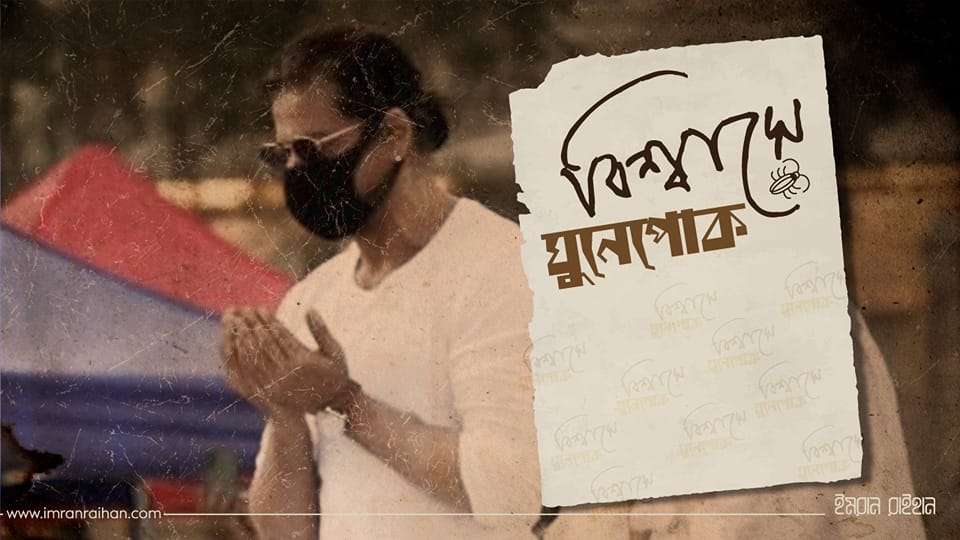জাফরাবাদ সৈয়দ মাস্টরের বাড়ি। বাগুড় বাজারে দাঁড়িয়ে যেকোন রিকশাওয়ালাকে বললেই চিনবে। ঠিক ঠিক বাড়ির রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিবে। পাকা রাস্তা থেকে বাম দিকে সোজা একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। দুইপাশে কাঠগাছ। গাড়ি থেকে নামলে মোড়েই একটা কবরস্থান। পারিবারিক কবরস্থান। এপিটাফে নাম লেখা সৈয়দ মাস্টর, ফাতেমা বানু, দুধ মিয়া। আজকে কবরস্থানে নতুন একটা কবর খোঁড়া হচ্ছে। এপিটাফ এখনো রেডি হয়নি।
কাঁচা মেঠো পথ দিয়ে শখানেক কদম সামনে এগোলেই বাড়ির আঙ্গিনা। তারপর বাড়ির শুরু। চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগানে ঘেরা। আঙ্গিনা পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার আগেই অনেকগুলো চেয়ার পাতা। দূর থেকে দেখতে পেলাম বড় মামা বসে আছেন। সাদা পাঞ্জাবি গায়ে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ধুপ করে সামনে একটি আম পরলো। আমের সিজনে এটা এই বাড়ির খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। হালকা বাতাসেই পাকা আম পরে। আর ঝড় এলে তো কথাই নেই। মামা বললেন, ভাগিনা আমটা নেও, তুমি আসছো, এটা তোমার রিযিক। আমটা হাতে নিতেই মনে হলো, আহারে এই বাড়িতে কোথাও একটা মরচে পরা সন্দুক আছে, যেখানে এমন বাতাসে পরা কাচাপাঁকা আমের একটা খাজানা লুকিয়ে রাখা হয়েছে।
আমি আম নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। দুই পাশে আড়াআড়ি টিন দিয়ে বাড়ির অন্দরমহলের উঠুন - পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা থেকে পথিকের দৃষ্টি আটকানোর চেষ্টা। নানার বাড়িতে ঢোকার পর শুরুতেই পরে সৈয়দ নানার বাড়ি। তারপর আমার আপন নানা দুধ মিয়ার বাড়ি। দুই বাড়ির দুই উঠানের চারপাশে মামাদের ঘর। নানাদের বাড়ি পেরুলেই হিন্দু বাড়ি। সৈয়দ নানার বাড়িতে ঢুকলেই চারটা ঘর ঘেড়া একটা উঠুন। তিন দিকে মাটির ঘর আর একপাশে একটা টিনের। উঠুনে একটা খাটিয়া রাখা। খাটিয়ার উপরটা লম্বা চাদর দিয়ে ঢাকা। ভেতরে আমার কাঁচাপাকা আমের সন্দুকের মালকিন সাদা কাপড় পরে ঘুমিয়ে আছেন। অন্য সময় বাতাসে আম পড়ার ধুপ শুনলেই যে মানুষটি দৌড়ে আসতেন সবার আগে, সেই মানুষটির চারপাশে আমের বাগান, ধুপধাপ বাতাসে কত আম পরছে, তার কোন হদিস নেই।
সন্দুকের মালকিন ফিরোজা বেগম। আমি ডাকি বন্নানি বলে। বড় নানি থেকে বন্নানি। বড্ড ভালোবাসার ডাক, আদরের ডাক। আমার নানা দুধ মিয়া। তার ভাই সৈয়দ মাস্টর। আমার আপন নানাকে আমি কখনো দেখিনি। জন্মের অনেক আগেই মারা গেছেন। আমার যে আপন নানা নেই সেটা আমি যথেষ্ট বড় হওয়ার আগে জানতামই না। কারণ সেই শুন্যতা কখনো বুঝতে দেননি যে মানুষটি তিনি হলেন আমার ছোট নানাভাই সৈয়দ মাস্টর। নবিয়াবাদ স্কুলে মাস্টারি করার সুবাদে এই নামে উনার ব্যাপক পরিচিতি। সৈয়দ নানার চেহারা ছিলো কিছুটা শেখ মুজিবের মতন।
আমার দুই নানা মিলে বিয়ে করেছিলেন চারটি। প্রতিজন দুটি করে। সবার শুরুতে আমার বড় নানা মানে আপন নানা মারা যান, তারপর ছোট নানার দ্বিতীয় বউ, ঐযে এপিটাফে যার নাম লেখা ফাতেমা বেগম, উনি। ছোট নানির গল্প অনেক শুনেছি মার কাছে। আমার জন্মের চল্লিশ দিনের মাথায় উনি মারা যান। মা আমাকে দেখাতে নিয়ে গেছিলেন নানিকে। নানি ঘোমটা সড়িয়ে আমাকে দেখছিলেন। এই গল্প মা প্রায়ই করতেন। তারপর মারা যান আমার আপন দুই নানি, প্রথমে বড় নানি, তারপর ছোটনানি। বছর তিনেক আগে সৈয়দ নানাও মারা গেলেন। শেষমেশ নানা বাড়িতে বাকি ছিলেন আমার একমাত্র নানি ফিরোজা বেগম, সৈয়দ নানার বড় বউ।
নানি ছিলেন ছিপছিপে গড়নের ছোট্ট একটা মানুষ। কত যে কাজ করতেন, কত যে কাজ করতেন তার ইয়ত্তা নেই। সকাল শুরু হওয়ার আগ থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার কাজ যেনো শেষই হয়না। এতবড় বাড়ির দেখাশোনা, আশেপাশের বাগানগুলো নিয়মিত ঝাড়ু দিয়ে পাতা কুড়ানো, সেই পাতা উঠুনজুড়ে শুকানো। ছোট লাকড়ি পেলে সেগুলোকে আলাদা করে শুকিয়ে লাকড়ির ঘরে রাখা, শুকানো লাকড়ি পাতা দিয়ে সারাদিন চুলা ঠেলে রান্না করা, রান্না শেষে চুলার কয়লা তোলে ছাই আর কাঠের কয়লা আলাদা করা, সেই লাকড়ির কয়লা দিয়ে দাঁত মেজে গোসল করতে করতে তার সন্ধ্যা গড়াতো। প্রতি সন্ধ্যায় গোসল নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই নানার ধমক খেতেন উনি। কিন্তু কোনভাবেই যে তার কাজ ফুরোয় না। আমি যখনই নানিকে দেখতাম, তার হাতে শলার ঝাড়ু। এই ঝাড়ুও হয়তো বানানো হয়েছে বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ের নারিকেল গাছ থেকে। এটা নিয়েও হয়তো তার প্রতি সপ্তাহে কিংবা মাসান্তে একটা হাঙ্গামা করতে হয়।
নানির কাজকর্ম ছিলো ভূতের মতন। মানুষটা দেখতেও ছিলেন কালো। সারাদিন থাকতেনও কালি-ঝুলি নিয়ে। কিন্তু এর মধ্যেও তার উপস্থিতি আশপাশ আলো করে রাখতো। কবর কবিতায় জসীমউদ্দিন যেমন বলেছিলেন,
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।
নানির একটা বিখ্যাত সন্দুক (সিন্দুক) ছিলো যেটা ছিলো একটা জাদুর বাকশো। কুড়িয়ে পাওয়া আমটা, সদ্য পাকা বেলটা, শুকনো বিস্কুটের ডিব্বাটা, মামাদের আনা চকলেটটা সবকিছুর স্থান হতো ঐ সন্দুকে। আর আমরা বেরাতে গেলে আমাদের জন্য সন্দুক থেকে বের হতো খাজানা। সেই খাজানাওয়ালা সন্দুক ছিলো নানার মাটির ঘরে লাগোয়া ছোট্ট একটা রুমে। যেখানে নানির আস্তানা ছিলো। সারাদিনই ঐ ঘরের মধ্যে উনি ঘুটুরমুটুর করে এটাওটা করতেন। ঐ ঘরে যাওয়া ছিলো আমাদের একদম মানা।
নানাদের ঘর ছিলো একটা লঙ্গরখানা। সারাদিনই সেখানে মেহমান থাকতো। এলাকার মসজিদের হুজুর, খালাতো বোনের ছেলে মেয়েরা - নানার চোখের সামনে থেকে পড়ালেখা করতো, মামাদের বন্ধুরা, এবং বেরাতে গেলে আমরা নিজেরাও শেকড় গাড়তাম নানাদের কোন একটা ঘরে। এই বাড়িতে প্রতিদিনই ডেগ ভরে রান্নাবান্না হতো। কতজন খায় তার তো হিসেবই নেই।
মজার বিষয় আগে আমরা যখন বেরাতে যেতাম, আমার আপন মামাদের ঘরে একটা ঢু দিয়েই চলে আসতাম সৈয়দ নানার ঘরে। এই ঘরে আমরা অলিখিত মেহমান। ঘরে গেলেই টেবিলে খাবার রেডি। যেহেতু আগে থেকে বলে কয়ে যেতাম না সুতরাং কপালে যা আছে তাই। মাইলার ডোগা, শুটকি, লাল মরিচের ভর্তা, পুকুরের মাছ আর কালেভদ্রে ভাগ্য সুপ্রশন্ন হলে মুরগির ঝোল। এখানে খেয়েদেয়ে রাত হলে নানাদেরই কোন একটা ঘরে চিপকা মেরে ঘুমিয়ে যেতাম।
আরো যখন ছোট ছিলাম, তখন মায়ের সাথে নানাবাড়িতে ঢোকার সময় কোন কারণে মা যদি আগে চলে যেতেন, আমি বাড়িতে না ঢুকে বাইরে বাগানে ঘুরঘুর করতাম। কারণ আমার লজ্জা লাগতো। তখন বাড়ির অন্দরমহল থেকে আমার খালিমনিরা আসতেন নিয়ে যেতে। আমি আরো লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম। আমার আপন খালাদের কখনো নানাবাড়িতে পেতাম না, কারণ তাদের সবাই বিবাহিত, যে যার সংসার নিয়ে আছে। কিন্তু সৈয়দ নানার ছেলেমেয়েরা সবে কলেজ ভার্সিটিতে পড়ে, সে হিসেবে সব খালা-মামাদের আদরই পেয়েছি।
মামা-খালা সব মিলিয়ে ছিলেন সাত আটজন। আমি আজ অবধি ঠিক মত জানিনা কে কার ঘরের সন্তান। কারণ বন্নানি এভাবেই সবাইকে আগলে রেখেছেন। ছোট নানি যেহেতু আগেই মারা গেছেন, উনার বাচ্চাকাদের মানুষ করার মহান দায়ীত্বও নানি নিজের কাধে তুলে নিয়েছিলেন। উনাদেরকে এমনভাবে রাখতেন যাতে করে কেউ আলাদা করতে না পারে। নিঃসন্দেহে উনি সফল হয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আজকে এতবছর পরও আমি ঠিকঠাক উনাদেরকে আলাদা করে চিনিনা।
নানির অসুখটা ধরা পরে বেশ কয়েকবছর আগে। কর্কট রোগ। যেই রোগের চিকিৎসা হয়না। হুট করেই একদিন মা বললেন, তোর নানির ক্যান্সার ধরা পরছে। ঢাকা-কুমিল্লা অনেক দৌড়াদৌড়ি। শেষমেশ বেশ কয়েকবার ইন্ডিয়াতেও নিয়ে যাওয়া হলো। এর ফাঁকে গতবছরের দিকে আমি নানিকে দেখতে গেলাম জাফরাবাদ। ঈদের ছুটি, সাথে আপারাও গেলো তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। নানিকে দেখে ঠিক চিনতে পারলাম না। শুকনা পাটকাঠি শরির এখন ভার দিয়েছে। চাপাভাঙ্গা গালে এখন মাংস চড়েছে। শ্যামবর্ণ মুখটা যেন গৌঢ়বর্ণের আভাস পাচ্ছে। নানিকে খুঁজে পেলাম তার হাসিতে। এখনো আলো ছড়ায়। খুব আদর করে আপাদেরকে বসালেন পাশে। বাচ্চাদের খোঁজ নিলেন। নানিকে দেখে বুঝারই উপায় নেই মরণঘাতি ক্যান্সারে আক্রান্ত। কথাবার্তা এখনো টনটনে। কোথায় যেনো একটু ক্লান্তির ছাপ। এছাড়া বাকিসব ঠিকঠাক। খালি এখন আর আগের মতোন দৌড়ে কাজ করতে পারেন না। মামিরা কোন কাজেই আর হাত দিতে দেননা। এই হতাশায় মনে হয় আরো খানিকটা কাবু হয়ে গেছেন। তৎনগদ কাজ করা এই শরিরের রিফ্লেক্স মাসল কি এত সহজে শিথিল হয়ে যাবে?
আমি গিয়েছিলাম এই রোজা শুরু হওয়ার একদিন আগে। ছোট মামা ইতালি থেকে বউবাচ্চাসহো দেশে এসেছেন নানিকে দেখতে। অনেক দিন পর মামার সাথে দেখা। উনি বেশ কয়েকমাস বাড়িতে ছিলেন। ঈদ করেই আবার ইতালিতে ব্যাক করেছেন। হাতে গুণে কয়েকদিন হলো মাত্র। এর মধ্যে আমারও আর যাওয়া হয়নি ওদিকে। মা দেখতাম প্রায়শই যেতেন নানিকে দেখতে। তার মধ্যে একদিন দুপুরে যোহরের পর খবর এলো নানি আর নেই। দুনিয়ার সকল ব্যস্ততার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। মা খবরটা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। উনি গত পরশুও উনাকে দেখে এসেছেন বেশ সুস্থসবল, টনটনে কথা বলছেন।
সব খালারা এসেছেন। সিলেট থেকে নানির বোনও এসেছেন। উনি বেশ কয়েক মাস নানির পাশে থেকেছেন। নানির সেবাযত্ন করেছেন। বাড়িভর্তি মানুষ। এত মানুষের আদর আপ্যায়নের দরকার আছে। মেহমানের যত্নআত্তি নিয়ে যেই মানুষটা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো সেই মানুষটার কোন বিকার নেই আজকে। চুপচাপ উঠুনের মাঝখানে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন।
রাত করে নানির জানাযা হলো। অন্ধকার রাতে কবরে নামিয়ে দিয়ে আসলাম আমার কালিঝুলির নানিটাকে। ছোট্ট তার দেহ। খাটিয়ায় কেউ ছিলো টেরই পাওয়া গেলো না।
ছিপছিপে গড়নের আমার ছোট্ট নানিটার মনে ছিলো সমুদ্রের বিশালতা। তার হাসিতে মুক্তো ঝড়তো। তাকে দেখলেই অন্তরে প্রশান্তি পেতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কবরটাকে তার মনের বিশালতার মতো প্রশস্ত করে দিবেন। আমার কালিঝুলির নানির কবরটাকে আলোকিত করবেন - আছড়ে পড়া নুরের আলো দিয়ে। তাকে ধৌত করবেন পানি, বরফ ও শিলা দিয়ে। তার কবরটা ছুঁয়ে থাকুক ঝড়ে পরা পাতারা, পরম মমতায়।